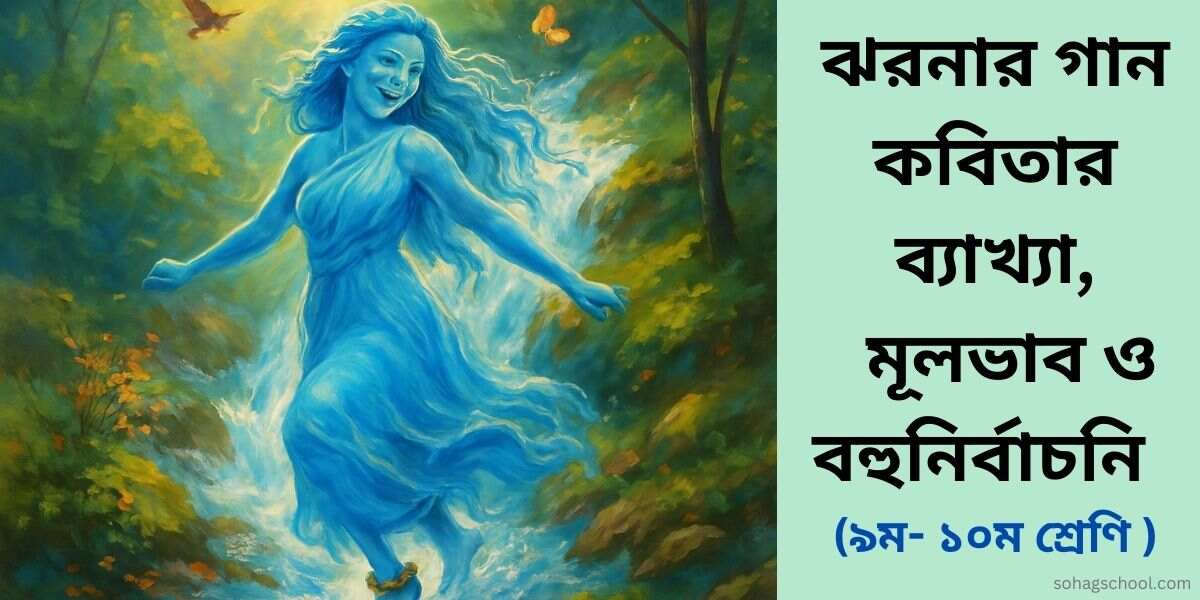সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ঝরনার গান’ একটি প্রকৃতিপ্রেমের কবিতা। কবিতায় ঝরনার চলাফেরা, চঞ্চলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা আর তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-পিপাসা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। এই পোস্টে ঝরনার গান কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা সহজ করে লিখে দিলাম।
Table of Contents
ঝরনার গান কবিতার মূলভাব
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ঝরনার গান’ কবিতায় একটি ঝরনাকে কবি জীবন্ত ও আনন্দময় রূপে উপস্থাপন করেছেন। ঝরনাটি যেন একটি চঞ্চল মেয়ে, যে পাহাড় থেকে নেমে আসছে আনন্দে নেচে গেয়ে। তার পায়ে যেন নূপুর বাঁধা, চলতে চলতে সে নিজের গান গায়। চারপাশে নির্জন দুপুর, পাখির ডাক নেই, বনভূমিও ঘুমিয়ে আছে—তবু সে একা একাই ছুটে চলে। পথে পথে পাথরের ওপর দিয়ে সে যায়, গায়ে ধাক্কা খায়, জল ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পাহাড় ভয় দেখালেও সে ভয় পায় না, বরং আরও জোরে দৌড়ায়। সে যেন কোনো পরীর উৎসবে নেমে আসা জলরাশি। ঝরনার জলে রঙের খেলা, আলো পড়ে তা ঝিলমিল করে। পাখি, গাছপালা আর পাহাড়ের মাঝে সে খেলে, লাফায়, ঘুরে বেড়ায়। তার গায়ে ঝোপঝাড়ের শেওলা লাগে, কিন্তু সে থামে না। তার গান, তার ছন্দ, সবই নিজস্ব, কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সে শুধু পান করার জল নয়, সে হলো সৌন্দর্যের এক উৎস। সে সেই মানুষের খোঁজে ছুটে চলে, যার চোখে সৌন্দর্য দেখার তৃষ্ণা আছে। সে যেমন গান গায়, তেমনই আশেপাশে আলো ছড়িয়ে দেয়। কবি এই ঝরনার মাধ্যমে প্রকৃতির জীবন্ত, চঞ্চল, সৃষ্টিশীল রূপটি তুলে ধরেছেন।
ঝরনার গান কবিতার ব্যাখ্যা
“চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।”
ব্যাখ্যা: কবি ঝরনাকে একজন প্রাণবন্ত, চঞ্চল ও সুরেলা জীবন্ত রূপে কল্পনা করেছেন। ঝরনা যেন তার চঞ্চল (চপল) পায়ে অবিরাম ছুটে চলে—কখনো থামে না। এই ছুটে চলা শুধু কোনো গতির প্রকাশ নয়, এর মধ্যে আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও প্রাণের জাগরণ আছে। ঝরনা যখন বয়ে চলে, তখন তার জলের ধ্বনি এমন মধুর লাগে যে মনে হয় সে যেন রূপকথার পরীদের গান গাইছে। এই গান শুনলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।
তার শরীরের প্রতিটি অংশে আনন্দের স্পন্দন—পুলক ছড়িয়ে আছে।
“শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝিঁর ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।”
ব্যাখ্যা: এখানে কবি ঝরনার চলার ভঙ্গিমা এবং পরিবেশের সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। ঝরনা যখন পাহাড় থেকে নিচে নামে, তখন সে পড়ে থাকে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে। ঝরনার পা—মানে তার জলের ধারা—এই পাথরের উপর পড়ে যেন নাচতে নাচতে চলে। এই চলা দেখে মনে হয়, তার মনও যেন দুলছে, দোদুল দোদুল করছে। কবির চোখে সেই সময়কার পরিবেশ খুব নির্জন—বেলা দুপুর হোক বা সকাল ভোর, চারপাশে কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। রাস্তা যেন অলস হয়ে এসেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। বন-জঙ্গলও যেন নিস্তব্ধতায় ডুবে ঘুমিয়ে আছে। এই ঘুমন্ত পরিবেশের মধ্যে শুধুই ঝরনার চঞ্চলতা—সে একা চলেছে, আর সবাই নিস্তব্ধ।
“বিজন দেশ, কূজন নাই
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।”
ব্যাখ্যা: ঝরনা যে পথে চলে, সে পথ খুবই বিজন—অর্থাৎ নির্জন, জনমানবশূন্য। সেখানে কোনো কূজন নেই, মানে পাখির ডাক বা অন্য কোনো জীবনের সাড়া নেই। চারপাশে এক নিস্তব্ধতা, এক গভীর নির্জনতা বিরাজ করে। এই একাকীত্বে ঝরনা কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ের শব্দে তালের মতো ছন্দ সৃষ্টি করে। আর এই ছুটে চলা শুধু দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সে দিন-রাত, সন্ধ্যা-সকাল সবসময়ই বয়ে চলে। যেন তার কখনোই বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই।
“ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়,”
ব্যাখ্যা: কবি বলছেন, ঝরনার জলের ধারা যেন ঝুম-পাহাড়ের দিকে ঝুঁকিয়ে, অথবা পাহাড়ের উপরে আছড়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে কিছুটা ভয়ের সৃষ্টি হয়, পাহাড় যেন তার বিশালতা ও শক্তি দিয়ে চোখ পাকিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। তবে ঝরনা কোনো ভয়েই থেমে থাকে না। সে শঙ্কা ছাড়া সমানভাবে চলে, যেন সে তার পথে অটুট, অবিচল, সাহসী। টগর ফুল ও নূপুর—যার অর্থ, এই ঝরনার পথের মাঝে এক সুন্দরতা, শোভা ফুটে ওঠে। কবি এখানে কিছু রূপক ব্যবহার করেছেন—টগর ফুলের মতো লাল, সুন্দর এবং নূপুরের মতো ঝঙ্কৃত সুর সৃষ্টি হচ্ছে ঝরনার চলার মধ্যে।
“কোন গিরির হিম ললাট
ঘামল মোর উদ্ভবে,
কোন পরীর টুটুল হার
কোন নাচের উৎসবে।”
ব্যাখ্যা: গিরির হিম—অর্থাৎ পাহাড়ের শীতল বরফ বা তুষারের গাঢ়তা, তার মধ্যে যেন এক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। এই উত্তাপ, এই শীতলতার ভেদ করে যেন ঝরনার জন্ম বা উদ্ভব হয়েছে। ঝরনা নিজে এক ধরনের শক্তি, এক ধরনের উত্সাহ, যা পর্বত থেকে নেমে এসে এক নতুন জীবন সৃষ্টি করে। কোন পরীর হার—অর্থাৎ এক রূপকথার পরী তার হার হারিয়ে ফেলেছে। এই হার হারানোটা যেন একটি গহীন নাচের উৎসবের অংশ। ঝরনা যেন সে উৎসবে অংশগ্রহণ করছে, যা শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং রহস্য ও মুগ্ধতারও সৃষ্টি করছে।
“খেয়াল নাই-নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়, খিলখিলাই-
বুলবুলির বোল সাধি।”
ব্যাখ্যা: কবি বলছেন, খেয়াল নাই-নাই রে ভাই, অর্থাৎ ঝরনা নিজের চলা বা গতির মধ্যে এতটাই মগ্ন যে, তাকে কোনো কিছুরই খেয়াল নেই, তাকে আর কিছু ভাবতে হয় না। সে নিজের গতিতেই চলে—কারও খবর বা সংবাদ তার কাছে পৌঁছায় না।
ঝরনার চলা যেন একটি লীলায় (এক ধরনের আনন্দময় গতিতে) ঘটছে। সে নিজে যখন ছুটে চলে, তখন তার মাঝে যেন একটি খিলখিল হাসির মতো আনন্দ ফুটে ওঠে। ঝরনার সুরে আবার বুলবুলির বোল বা গানের মতো একটা মধুরতা তৈরি হচ্ছে, যেটি যেন তার চলার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। বুলবুলের গান বা সুর—ঝরনার সঙ্গী হয়ে তার ছুটে চলার পথে একটি মধুর, সুরেলা পরিবেশ সৃষ্টি করছে।
“বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কালসারের দল চরে,
শিং শিলায়-শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে।”
ব্যাখ্যা: বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়—অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে ঝাউগাছের ঝোপে অনেক পাখি বা প্রাণী বাস করে। এখানে কবি কালসার পাখির দল বলছেন, যারা প্রকৃতির মাঝে খুঁজে বেড়ায়, উড়ে চলে। তারপর কবি বলছেন, শিং শিলায়-শিলার গায়, অর্থাৎ কোনো হরিণ বা অন্য কোনো প্রাণী তার শিং নিয়ে পাথরের গায়ে আঁচড় কাটছে বা খুঁচিয়ে চলেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে ডালচিনি—একটি মসলার রঙ থাকে, তার মতো এক ধরনের বিশেষ রঙের ধারা এই দৃশ্যের মধ্যে মিশে রয়েছে।
“ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাঁট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই-
টিলার গায় ডালিম-ফাট।”
ব্যাখ্যা: ঝরনার স্রোত যে কোনো বাধাকে ডিঙিয়ে, ঝাঁপিয়ে বা লাফিয়ে চলে। ঝরনা যেন এক আনন্দে পাথরের ওপর লাফিয়ে পড়ে, কোনো থামানো প্রয়োজন নেই। দুলিয়ে যাই অচল-ঠাঁট—এখানে “অচল-ঠাঁট” শব্দবন্ধ দিয়ে কবি সম্ভবত এমন বস্তু বা দৃশ্যের কথা বলছেন, যেগুলি স্থির এবং শান্ত। যেমন কিছু স্থির পাথর বা শক্ত বস্তু ঝরনার স্রোত দ্বারা দুলিয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে তার গতির শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে।
ঝরনার গতি এতটাই প্রবল যে, তা নাচাতে এবং বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির প্রতিটি অংশ, যেন তার স্রোত বা তরঙ্গ সবাইকে স্পর্শ করছে।
টিলার গায় ডালিম-ফাট—এখানে “টিলা” বলতে ছোট পাহাড় বা বুকে বড় বড় পাথর নিয়ে উঠতি ভূমি বোঝানো হয়েছে। সেই টিলার উপরে যেমন ডালিম ফলের মতো রঙিন দাগ বা আঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ, ঝরনার শক্তি এতটাই প্রবল যে সে টিলার গায় ফাটলও ধরিয়ে দেয়।
“শালিক শুক বুলায় মুখ
থল-ঝাঁঝির মখমলে,
জরির জাল আংরাখায়
অঙ্গ মোর ঝলমলে।”
ব্যাখ্যা: এখানে শালিক পাখির কথা বলা হচ্ছে, যারা মিষ্টি গলায় গান গাইতে পারে। কবি বলতে চাচ্ছেন যে, এই পাখির মুখ থেকে কিছু শব্দ বের হচ্ছে বা সে গান গাইছে। শুক ও শালিকের গান এমন এক পরিবেশে শোনা যাচ্ছে, যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং কোমলতা মিলিত হয়ে এমন এক আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করছে যা মনোমুগ্ধকর। জরি হল এক ধরনের সুতির অথবা রেশমের কাজ, যা পোশাকের শোভা বাড়ায়। কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে ঝরনার অঙ্গ বা শরীর যেন রেশম বা জরির কাজের মতো ঝলমলে, বা এক ধরনের ঝলমলে গ্লিমার নিয়ে ঝলকাচ্ছে।
“নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
‘ফটিক জল।’ হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক না সেই পাঁক ছেঁকে।”
ব্যাখ্যা: ঝরনার স্রোত যখন নিচে নামে, তখন কবি তার স্রোতের শব্দ শোনেন এবং অনুভব করেন। ঝরনার পানি যখন নিচে গিয়ে পড়ে, তখন সেটি একটা নির্দিষ্ট গর্জন বা ধ্বনি তৈরি করে, যেটি কবির মনে নতুন কল্পনা জাগিয়ে তোলে।
‘ফটিক জল’ মানে চাতক পাখি। এই পাখি ডাকলে ‘ফটিক জল’ শব্দের মতো শোনা যায়। এই পাখি যেন পানি বা তৃষ্ণার জন্য ডাকছে।
এই পাখি মাটির গভীরে পানি খোঁজার চেষ্টা করছে। কবি এমনভাবে প্রকৃতির মাঝে সেই তৃষ্ণার অবস্থা অনুভব করছেন, যেখানে প্রকৃতি নিজেই জল খোঁজে, তার শান্তি বা তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না।
“গরজ যার জল স্যাঁচার
পাতকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।
তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান-তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,”
ব্যাখ্যা: কবি বলছেন, যে জীব বা প্রাণী তৃষ্ণায় ভুগছে, তার তৃষ্ণা কখনোই পুরোপুরি মেটে না, কারণ সৌন্দর্য বা তৃষ্ণা এক অবিরাম আকাঙ্ক্ষা। কবি এখানে বলেন, যে জীবের সুন্দর তৃষ্ণা আছে, আমরা তার পিছনে ছুটে চলি, এবং তার খোঁজে কখনো থামি না। কবি চকোর পাখি এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যেমন চকোর পাখি চাঁদের আলো চায়, তেমনি আমাদেরও সুন্দর বা আদর্শের প্রতি একটি অবিরাম আকাঙ্ক্ষা থাকে, যা কখনো শেষ হয় না।
“আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।
চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক।”
ব্যাখ্যা: আমরা এমন এক সৌন্দর্য বা অভিজ্ঞতা চাই, যা আমাদের মুগ্ধ করবে, আমাদের চোখে নতুন আলো নিয়ে আসবে। চপল (অতি গতিময় বা চঞ্চল) পাখি, যেমন ছুটে চলে, তেমনি তার মনের মতো কিছু পেতে সে অবিরত ছুটে চলে।
পাথরে আঘাতের পর যে ঝিলিক দেখা দেয়, ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে সৌন্দর্য বা আবেগের ঝিলিক সবসময় উপস্থিত থাকে। এরপর জীবন বা সৌন্দর্য মানুষের মনকে আছড়ে ফেলে, দোলনা বা ঝিমিয়ে যাওয়ার মত তার মনকে প্রভাবিত করে, এবং ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক, যা পৃথিবীকে এক ধরনের মিলানো, মাধুর্যপূর্ণ পরিবেশে পরিণত করে।
আরও পড়ুনঃ জীবন বিনিময় কবিতার মূলভাব ও সহজ ব্যাখ্যা