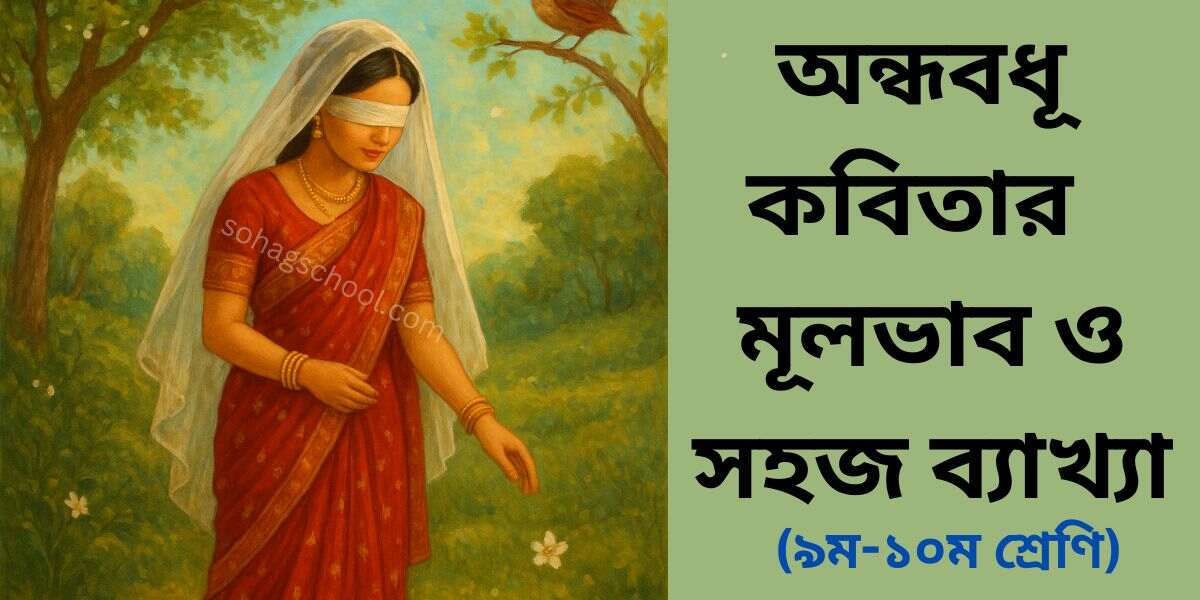যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘অন্ধবধূ’ কবিতাটি এক অন্ধ মহিলার জীবনের গল্প। কবিতার মধ্যে সেই মহিলার অনুভূতি, তার দুঃখ-কষ্ট, তার আশঙ্কা এবং তার জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা উঠে এসেছে। এই পোস্টে অন্ধবধূ কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা লিখে দিলাম।
Table of Contents
অন্ধবধূ কবিতার মূলভাব
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “অন্ধবধূ” কবিতাটি একটি অন্ধ বধূর জীবনের গল্প বলে, যার অনুভূতি এবং ভাবনা অত্যন্ত গভীর। কবিতার শুরুতে, এই বধূটি তার পায়ের তলায় নরম কিছু অনুভব করে এবং মনে করে, এটি ঝরা বকুল ফুল। সে বুঝতে পারে, প্রকৃতি তার চারপাশে পরিবর্তন হচ্ছে এবং নতুন ঋতুর আগমন ঘটছে। সে জানে কোকিলের ডাক শুনলে বুঝা যায় ঋতু বদলাচ্ছে। যদিও সে অন্ধ তবে তার অবচেতনা শক্তি এত প্রখর যে সে বাকি সবকিছু অনুভব করতে পারে। কবিতায় সে তার অন্ধত্ব নিয়ে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না করে বরং জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ দেখায়। একসময় সে তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং মনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। যেখানে সে ভাবে, ডুবে মারা গেলে হয়তো অন্ধত্বের শাপমুক্তি ঘটবে। তবে কবিতায় তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি স্পষ্ট যে, সে জীবনের প্রতি কোনো নৈরাশ্য বোধ করে না বরং সে জানে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সে পৃথিবীকে উপলব্ধি করে। সে তার শোককে সহ্য করে এবং জীবনকে শক্তি দিয়ে বাঁচতে চায়। কবিতায় অন্ধবধূর শক্তি এবং তার অনুভূতি শক্তি সমাজের জন্য একটি শিক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যা আমাদেরকে শিখায় যে, দৃষ্টিহীন হলেও একজন মানুষ নিজের অনুভূতির মাধ্যমে পৃথিবীকে পুরোপুরি বুঝতে পারে।
অন্ধবধূ কবিতার ব্যাখ্যা
পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি-
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল। নয়?
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, অন্ধবধূটি পায়ের তলায় মাটির নরম অনুভব করছে এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে চাইছে। তিনি তাঁর ননদ বা স্বজনকে ডেকে বলেন “আস্তে একটু চল।” পথের ধাপে ধাপে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করছেন। এরপর তিনি লক্ষ্য করেন, ঝরে পড়া বকুলের ফুল তার পথে পড়েছে। অর্থাৎ, অন্ধবধূর অন্তর্দৃষ্টি ও স্পর্শশক্তি তাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরতে সাহায্য করছে, যদিও সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না।
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল- মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল- কতই মনে হয়।
জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই-
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
কবি এখানে বলছেন, অন্ধবধূটি দরজার পাশে বসে ভাবছে। রাতের অন্ধকার, মধুর সুগন্ধে ভরা পরিবেশ, আকাশ-পাতালের নানা রঙ ও অনুভূতি তাঁর মনে হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, জ্যৈষ্ঠ মাস (গরম ঋতু) আসতে কতদিন বাকি। আমের গাছে বরণ (ফুল বা ফলের আভা) কখন দেখা যাবে তা অনুমান করতে চাইছেন। অর্থাৎ, অন্ধবধূর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি এত শক্তিশালী যে, চোখ না দেখলেও সে ঋতুর পরিবর্তন, প্রকৃতির রূপ-রস বুঝতে পারে।
অনেক দেরি? কেমন করে হবে।
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া বন্ধকবে ভাই;
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, অন্ধবধূটি ভাবছে জ্যৈষ্ঠ আসতে অনেক দেরি হবে কি না, তা সে জানতে চাচ্ছে। সে মনে করছে, কোকিলের ডাক শুনেছে অনেক আগে, কিন্তু দক্ষিণ দিকের হাওয়া (দক্ষিণ হাওয়া) এখনও বন্ধ। অর্থাৎ, সে ঋতুর আগমন বা প্রকৃতির পরিবর্তনকে তার শ্রবণ ও অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করছে। চোখ না থাকা সত্ত্বেও তার অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভব বোঝায়।
দীঘির ঘাটে নতুন সিড়ি জাগে-
শ্যাওলা-পিছল এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!
মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায়-
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, অন্ধবধূটি দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শঙ্কিত বোধ করছে। শ্যাওলা পড়ে সিঁড়ি পিছল, তাই ভয় হচ্ছে। পা পিছলে সে জলে পড়ে যেতে পারে। যদিও সাধারণভাবে এটি খুব গুরুতর ঘটনা নয়, তার অন্ধ চোখের জন্য এটি একটি গভীর দ্বন্দ্ব ও আতঙ্ক তৈরি করছে। অর্থাৎ, অন্ধবধূর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, তার অনুভূতি, সতর্কতা এবং আতঙ্কের প্রকাশ তাকে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে জড়িত করে রাখে।
দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, অন্ধবধূর চারপাশের মানুষ তাকে ধৈর্য ধরতে এবং সবকিছু ঠিক থাকবে ভেবে বোঝাচ্ছে। তারা বলে, “দুঃখ নেই, সত্যি কথা শোন, অন্ধ হয়ে গেলেও কী হবে?” তাঁর স্বামীর বাঁচার কথা বলা হচ্ছে—“তোমরা বাঁচবে তো, দাদা, তোর আগে।” আবার উল্লেখ করা হচ্ছে, এই আষাঢ় মাসেই (বর্ষা ঋতু) বিয়ে হবে, অর্থাৎ জীবনের নিয়মিত ঘটনাগুলো চলতে থাকবে। এটি দেখায়, অন্ধত্ব সত্ত্বেও জীবনের চলমান ধারা অব্যাহত থাকে এবং পরিবার আশ্বাস দেয়।
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে-
দেখবি তখন প্রবাস কেমন লাগে?
‘চোখ গেল’ ওই চেঁচিয়ে হলো সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা-
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, অন্ধবধূর দৃষ্টিহীন অবস্থায় সে নিজেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। তখন সে প্রবাসের মতো নিঃসঙ্গ ও অসহায় অনুভব করবে। চারপাশের “চোখ গেল! পাখি চেঁচিয়ে বোঝাচ্ছে যেন তার অন্ধত্ব সবাই জানে। কবি প্রশ্ন করছেন, এমন পরিস্থিতিতে দিদি বা ভাইরা কী করবে, অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতি ও সাহায্য কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে।
জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার ছাই!
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কমত যে তার শোক।
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, যে ব্যক্তির চোখ জন্মের পর থেকে অন্ধ, তার জীবনদৃষ্টি অন্যদের মতো নয়। সাধারণ মানুষ হয়তো বলে, “কাঁদার সুখ তার জন্য নিষিদ্ধ”। কিন্তু অন্ধবধূ যদি কাঁদতে পারত, তার শোক কিছুটা হলেও হ্রাস পেত। অর্থাৎ, চোখ না থাকার কারণে তার দুঃখ আরও গভীর এবং অনুভূতিশীল। কবি মানব জীবনের দুঃখ-বেদনা ও অন্ধত্বের মানসিক প্রভাবকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন।
‘চোখ গেল’- তার ভরসা তবু আছে-
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!
টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি-
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, ‘চোখ গেল’ পাখির কিছু ভরসা আছে। সে জানে, চক্ষুহীন হওয়ায় কি অন্যদের কাছে তার কথা খুব বেশি মূল্য রাখে না, তবুও আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। তার ননদ তাকে টানতে চায় বা তাড়াহুড়া করে এগিয়ে নিতে চায়, সে বলছে—কেন এতো তাড়াহুড়া? শেষ পর্যন্ত সে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে। অর্থাৎ, অন্ধবধূ নিজের সক্ষমতা এবং জীবনের পথে আত্মবিশ্বাস ধরে রেখেছে।
একলা-থাকা- সেই তো গৃহকোণ-
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে-
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত।
কবি এখানে দেখাচ্ছেন, একা থাকা মানেই অন্ধবধূর জন্য শুধু ঘরের কোণ নয়। বরং, শীতল নদী বা জলের স্নিগ্ধতায় সে প্রাণের কথা অনুভব করতে পারে। সেই জলে যেন দু’টি প্রাণ একে অপরের সঙ্গে আলাপ করছে। দুঃখ-দরদ ভাগাভাগি করছে। জলের স্পর্শ যেন মায়ের স্নেহের মতো, যা তার মনের ব্যথা কিছুটা ভুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ, প্রকৃতি ও স্পর্শের মাধ্যমে অন্ধবধূ মানসিক স্বস্তি এবং সংযোগ অনুভব করছে।
আরও পড়ুনঃ প্রাণ কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা খুব সহজ ভাষায়