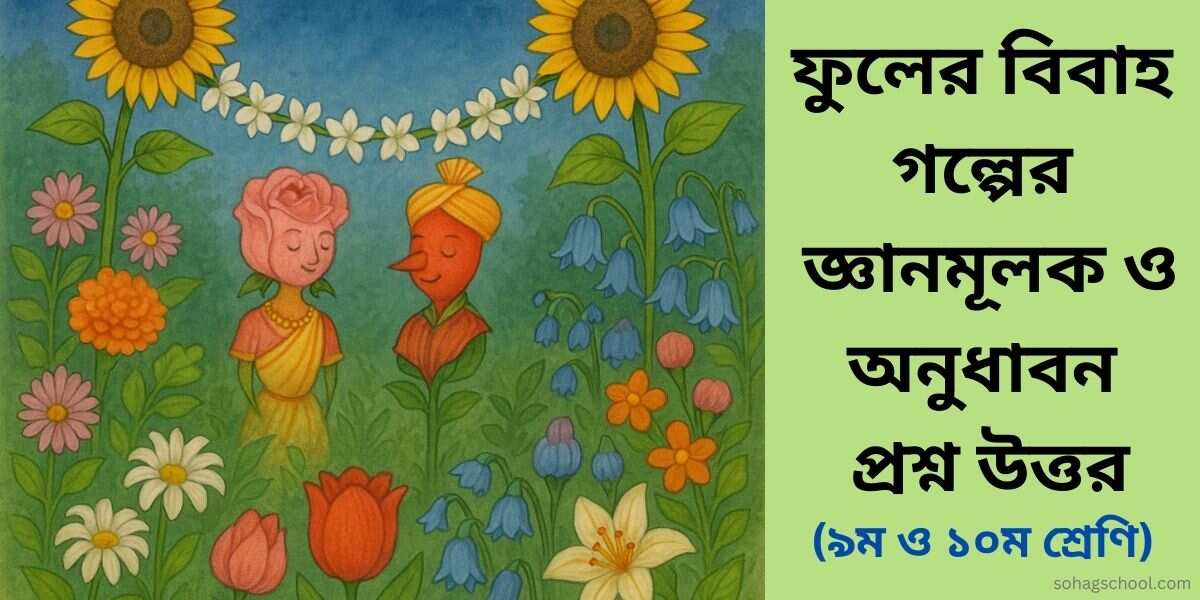“ফুলের বিবাহ” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই রূপকথাধর্মী ছোটগল্পটিতে ফুলের বিবাহের প্রস্তুতি, ঘটকের সম্বন্ধ-চেষ্টা, বরযাত্রীদের আগমন, এবং শেষে সুতোয় গাঁথা ফুলমালার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার দৃশ্য কবিত্বময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই পোস্টে ফুলের বিবাহ গল্পের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর লিখে দিলাম।
Table of Contents
ফুলের বিবাহ গল্পের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন
১। ‘ফুলের বিবাহ’ গল্পের লেখক কে?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। ‘ফুলের বিবাহ’ রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর: ‘ফুলের বিবাহ’ রচনাটি কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের নবম সংখ্যক লেখা।
৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ কত?
উত্তর: ২৬শে জুন, ১৮৩৮।
৫। বঙ্কিমচন্দ্র কোন সালে বি.এ. পাশ করেন?
উত্তর: ১৮৫৮ সালে।
৬। বঙ্কিমচন্দ্র বি.এ. পাশ করার পর কোন পদে নিযুক্ত হন?
উত্তর: ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে।
৭। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কী?
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী।
৮। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ কবে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৬৫ সালে।
৯। ‘লোকরহস্য’ গ্রন্থটি কোন সাহিত্যরূপের অন্তর্গত?
উত্তর: প্রবন্ধসাহিত্য।
১০। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু কবে হয়?
উত্তর: ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪।
১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হন?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩। ফুলের বিবাহ’ গল্পটির কাহিনি কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা?
উত্তর: ফুলের কল্পিত বিবাহ।
১৪। পাত্রী কে ছিল?
উত্তর: মল্লিকা ফুল।
১৫। বর কে ছিল?
উত্তর: গোলাব (গোলাপ) ফুল।
১৬। ঘটক কে ছিল?
উত্তর: ভ্রমর (মৌমাছি)।
১৭। ‘পরিমল’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: সুগন্ধ বা সুন্দর গন্ধ।
১৮। মল্লিকার পিতা কে?
উত্তর: মল্লিকা বৃক্ষ।
১৯। স্থলপদ্মকে পাত্র হিসেবে কেন বাতিল করা হয়?
উত্তর: তাঁর ঘর উঁচু হওয়ায়।
২০। জবাকে কেন বেছে নেওয়া হয়নি?
উত্তর: সে রাগী ছিল বলে।
২১। গন্ধরাজকে কেন বাদ দেওয়া হয়?
উত্তর: অহংকারী হওয়ার জন্য।
২২। ঘটক কাকে দেখতে চায়?
উত্তর: পাত্রীকে।
২৩। ‘অবগুণ্ঠনবতী’ বলতে কেমন নারীকে বোঝানো হয়?
উত্তর: ঘোমটা দেওয়া বা মুখ ঢাকা নারীকে।
২৪। পাত্রী প্রথমে মুখ দেখায়নি কেন?
উত্তর: লজ্জায়।
২৫। পাত্রীকে কে বোঝায় মুখ দেখাতে?
উত্তর: সন্ধ্যা ফুল।
২৬। পাত্রী মুখ দেখানোর পর ঘটকের মন্তব্য কী ছিল?
উত্তর: “কন্যা গুণবতী বটে।”
২৭। বর যাত্রার দিন কোন তারিখে ছিল?
উত্তর: ১লা বৈশাখে।
২৮। ‘কমলকাকা’ কাকে বলা হয়েছে?
উত্তর: কমলাকান্তকে কাকা বলে সম্বোধন করে কমলকাকা বলা হয়েছে।
২৯। বর যাত্রা কোথা থেকে শুরু হয়?
উত্তর: গোলাব ফুলের বাসস্থান থেকে।
৩০। বর যাত্রার বাহক কে হওয়ার কথা ছিল?
উত্তর: বাতাস।
৩১। বরযাত্রায় কারা কারা অংশ নিয়েছিল?
উত্তর: জবা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, বকুল প্রমুখ।
৩২। কন্যাকে কে বরণ করে?
উত্তর: ফুলেরা (যুঁই, বকুল, মালতী প্রভৃতি)।
৩৩। পুরোহিতের কাজ কে করে?
উত্তর: নসী বাবুর কন্যা কুসুমলতা।
৩৪। গাঁটছড়া বাঁধার কাজ কে করে?
উত্তর: কুসুমলতা।
৩৫। ‘খদ্যোত’ বলতে কোন পোকাকে বোঝায়?
উত্তর: জোনাকি পোকাকে।
৩৬। গাঁটছড়া কী দিয়ে বাঁধা হয়?
উত্তর: সুতো দিয়ে।
৩৭। ভ্রমরের ‘গুণ গুণ’ ধ্বনি কী বোঝায়?
উত্তর: মৌমাছির গুঞ্জন।
৩৮। ‘ফুলে মেল’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ফুলের উজ্জ্বল ও খ্যাতিসম্পন্ন বংশ।
৩৯। বরকে নিয়ে কে ব্যঙ্গ করে?
উত্তর: রঙ্গন ও অন্য ফুলেরা।
৪০। বাসরঘরে পাত্রীকে ঘিরে কারা ছিল?
উত্তর: ফুলসুন্দরীরা।
৪১। রজনীগন্ধাকে বর কী নামে ডাকে?
উত্তর: তাড়কা রাক্ষসী।
৪২। ‘ইয়ারকি’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: রসিকতা বা ফাজলামি।
৪৩। বকুল ফুলের স্বভাব কেমন?
উত্তর: গুণ আছে, রূপ কম।
৪৪। ঝুমকা ফুল কেমন আচরণ করে?
উত্তর: মোটা গৃহিণীর মতো জমকালো বসে।
৪৫। মালা গাঁথার মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ফুলের বিবাহের বাস্তব রূপ।
৪৬। ‘পত্রাসন’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: পাতার ওপর বসার আসন।
৪৭। গল্পে হাস্যরস কোথায় বেশি প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর: ঘটক ভ্রমর ও বরযাত্রার বর্ণনায়।
৪৮। স্থলপদ্ম কেন সম্বন্ধে আগ্রহ দেখায় না?
উত্তর: কারণ তার “ঘর বড়ো উঁচু” (সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান)।
৪৯। খদ্যোত (জোনাকি) কী কাজ করে?
উত্তর: বিবাহের আলোকসজ্জার দায়িত্বে থাকে।
৫০। কন্যার ঘোমটা খোলার জন্য কে তাকে রাজি করায়?
উত্তর: সন্ধ্যাঠাকুরাণী (সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা)।
৫১। ঘটক ভ্রমর কী চায়?
উত্তর: “মধু”
৫২। বরযাত্রীদের মধ্যে উৎপাতকারী কে?
উত্তর: পিঁপড়ার দল
৫৩। বাতাস কেন বরযাত্রীদের সাহায্য করে না?
উত্তর: কাজের সময় “লুকিয়ে” যায়
৫৪। কুসুমলতা কে?
উত্তর: নসী বাবুর ৯ বছর বয়সী কন্যা, যে ফুলমালা গেঁথে বিবাহ সম্পন্ন করে।
৫৫। “ফর্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিবে”—এটি কার উক্তি?
উত্তর: মল্লিকা ফুলের পিতা (ক্ষুদ্র বৃক্ষ)।
৫৬। গোলাপ কেন “বাঞ্ছামালির সন্তান”?
উত্তর: হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গোলাপ বিষ্ণুর বাঞ্ছামালি (ইচ্ছেপূরণকারী মালা) থেকে জন্মেছে।
৫৭। “ফুলের বিবাহ” গল্পে কোন ঋতুর উল্লেখ আছে?
উত্তর: বৈশাখ (গ্রীষ্ম)।
৫৮। “সেঁউতি” কী ভূমিকা পালন করে?
উত্তর: নীতবর (বরযাত্রী)।
৫৯। গল্পে “টগর” ফুলের ভূমিকা কী?
উত্তর: প্রাচীনা ঠাকুরাণী, যিনি রসিকতা করেন।
৬০। “ফুলের বিবাহ” গল্পের সময়কাল কতক্ষণ?
উত্তর: একটি বৈশাখের সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত।
৬১। ‘কন্যাভারগ্রস্ত’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বিবাহযোগ্যা কন্যা বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি।
৬২।’সম্বন্ধের’ শব্দের মানে কী?
উত্তর: বিয়ের সম্পর্ক সংক্রান্ত।
৬৩। ‘কন্যাকর্তা’ কাকে বলে?
উত্তর: কন্যার অভিভাবককে কন্যাকর্তা বলে।
৬৪। ‘সন্ধ্যাঠাকুরাণী দিদি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: এখানে সন্ধ্যাকে দিদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এটি অলংকারমূলক ভাষা।
ফুলের বিবাহ গল্পের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর
১। কলিকা-কন্যাকে বিয়ের যোগ্যা বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
মল্লিকা একটি ফুলের গাছ। তার একটি কলিকা অর্থাৎ কুঁড়ি বয়সে পরিপক্ব হতে চলেছে। এই বয়সে একটি ফুল তার সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়াতে প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতির সময়টিকেই লেখক কাব্যিকভাবে ‘বিয়ের যোগ্যা’ বলে বর্ণনা করেছেন। ফুলের জীবনের এই রূপান্তরকাল মানবজীবনের যৌবনের মতো। তাই লেখক কলিকা-কন্যাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে পরিপক্ব মনে করেছেন। এজন্য তার ‘বিবাহের’ আয়োজন কল্পনা করেছেন।
২। “বৃক্ষ শাখা নত করিয়া মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।” – এখানে ‘মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
‘মুদিতনয়না’ মানে যার চোখে আনন্দ ফুটে উঠেছে। ‘অবগুণ্ঠনবতী’ মানে যিনি ঘোমটা বা পর্দা টেনে রেখেছেন। এখানে ফুল-কন্যাটি লজ্জাশীলা, ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকেছে, কিন্তু চোখে তার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে। সে যেমন লাজুক, তেমনি বিয়ের প্রসঙ্গে উৎসাহিত। লেখক কল্পনার ভঙ্গিতে ফুলের স্বভাবকে মানবিক রূপ দিয়েছেন। এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে ফুলের কোমলতা, লজ্জা ও মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
৩। গোলাবকে কুলীন বংশ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গোলাব মানে গোলাপ ফুল, যাকে লেখক খুব মর্যাদাশালী ফুল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পে বলা হয়েছে গোলাপ ‘বাঞ্ছামালির সন্তান’, অর্থাৎ এক বিশেষ মালি তাকে রোপণ করেছেন। এতে বোঝানো হয়েছে, তার জন্ম বংশমর্যাদাসম্পন্ন স্থানে। লেখক কল্পনাপ্রবণ ভঙ্গিতে গোলাপের অতুল সৌন্দর্য, সুগন্ধ এবং জনপ্রিয়তাকে ‘কুলীন’ অর্থাৎ অভিজাত বংশের প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। তার চারিত্রিক গুণ, গন্ধ, ও ঐতিহ্য তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এজন্য গোলাবকে কুলীন বংশের বলা হয়েছে।
৪। ফুলের বিয়েতে মৌমাছি কেন যেতে পারেনি?
মৌমাছি ফুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও সে এই বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেনি। কারণ গল্পে বলা হয়েছে, মৌমাছি ‘রাতকানা’, অর্থাৎ সে অন্ধকারে ভালো দেখতে পায় না। বিয়েটি সন্ধ্যায় বা রাতে হওয়ায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে সানাই বাজানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, কিন্তু সময়মতো যেতে না পারায় বাদ পড়েছে। এই ঘটনাটি কল্পনাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হলেও মৌমাছির প্রকৃতিগত আচরণের সঙ্গে মিল রয়েছে। এতে লেখক একটি কৌতুকমিশ্রিত দুঃখময় আবহ সৃষ্টি করেছেন।
৫। “আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল।” – ব্যাখ্যা কর।
এই বাক্যটি ফুলের বিয়ের আনন্দঘন পরিবেশকে রঙিনভাবে তুলে ধরেছে। এখানে ‘আকাশে তারাবাজি’ বলতে বোঝানো হয়েছে সন্ধ্যা আকাশে তারা একে একে জ্বলে উঠেছে। বাস্তবে তারার জ্বলে ওঠা একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও লেখক তা ‘তারাবাজি’ অর্থে ব্যবহার করে উৎসবের ছবি এঁকেছেন। এতে ফুলের বিয়েকে মানুষের বিয়ের মতো আনন্দপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। গল্পের কল্পনাপ্রবণ ভঙ্গিমায় এই রূপক ব্যবহৃত হয়েছে। এতে পাঠকের মনে একটি রূপকথার পরিবেশ তৈরি হয়।
৬। করবীর দলকে সেকেলে রাজাদের সাথে তুলনা করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গল্পে করবীর দলকে ‘সেকেলে রাজাদের মতো’ বলা হয়েছে। কারণ, তারা বড় বড় ডালে উঠে রাজকীয় ভঙ্গিতে এসেছে। এ থেকে বোঝা যায়, তারা অত্যন্ত গর্বিত, আড়ম্বরপূর্ণ ও চটকদারভাবে প্রবেশ করেছে। তাদের উপস্থিতি একটি প্রাচীন কালের রাজবাহিনীর মতো ছিল। ফুলের বিয়েকে আরও জমকালো দেখাতে এই তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে লেখক কল্পনার ছোঁয়ায় প্রকৃতিকে রাজকীয় নাট্যরূপ দিয়েছেন।
৭। “আর কোন বিবাহে না তাহারা ফুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়?” – পিঁপড়া সম্পর্কে এরূপ বলার কারণ লেখ।
এই বাক্যে পিঁপড়ার স্বভাব কৌতুকপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পিঁপড়ারা মিষ্টি ও ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয় এবং প্রায়ই ফুলের পাঁপড়ি কেটে দেয় বা ক্ষতি করে। ফুলের বিয়ের সময়ে তাদের এমন আগমন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে লেখক বলেছেন তারা “ফুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়”। এ যেন প্রতিটি আনন্দঘন মুহূর্তে কেউ না কেউ গোলমাল পাকায়—এই মানবিক বাস্তবতার প্রতীক। লেখক কল্পনার ছোঁয়ায় পিঁপড়াদের বিরোধী পক্ষ রূপে দেখিয়েছেন। এতে বিয়ের গল্পে একটি মজার মোড় ও নাটকীয়তা এসেছে।
৮। ঘোমটা না খুললে বর কেন আসবে না? – ব্যাখ্যা কর।
বিয়ের রীতি অনুযায়ী কনে যদি মুখ না দেখায়, তাহলে বর কনেকে দেখতে পায় না। গল্পে ফুল-কন্যা যদি মুখ না দেখায়, তাহলে বর ফুল-কন্যাকে চিনবে না—এই ভাবেই তা উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘ঘোমটা’ এখানে লজ্জা, রহস্য এবং রূপের প্রতীক। লেখক কল্পনায় কনেকে একটি রুচিশীল চরিত্রে দেখিয়েছেন, যার মুখ দেখাই যেন বিয়ের একটি প্রধান অংশ। বর শুধু রূপেই আকৃষ্ট নয়, ভালোবাসা ও পরিচয়ের প্রতিও আগ্রহী। তাই ঘোমটা না খুললে বর আসবে না—এমন কথা বলা হয়েছে।
৯। ঘটন মশায়ের সবখানে যাতায়াতের কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘটক মশায় অর্থাৎ ঘটক বা বিয়ের মধ্যস্থতাকারী সবখানে যাতায়াত করেন, কারণ তাকে পাত্র ও পাত্রীর পরিবার সম্পর্কে খোঁজ রাখতে হয়। গল্পে তাকে ফুল ও গন্ধের মাঝে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এতে বোঝানো হয়েছে, ঘটক মশায় শুধু সামাজিক নয়, প্রকৃতির মধ্যেও বিবাহের যোগসূত্র তৈরি করেন। লেখক হাস্যরসের ভঙ্গিতে ঘটককে এমন ব্যক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন, যিনি সর্বত্র বিচরণ করেন। বিয়ের আয়োজনকে সফল করাই তার মূল লক্ষ্য। তাই তিনি সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন।
১০। “আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে।” – ব্যাখ্যা কর।
এই বাক্যে ফুল-কন্যার বিয়ের আনন্দ চিত্রিত হয়েছে। সে লজ্জা ভুলে গিয়ে ঘোমটা সরিয়েছে, মুখ ফুটেছে—এ মানে সে খুশিতে নিজের সৌন্দর্য ও সুবাস (পরিমল) ছড়াচ্ছে। আনন্দে তার মন ভরে গেছে, তাই সে হাসছে। এই হাসি নিছক মুখের নয়—এটি অন্তরের পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রকাশ। এখানে ফুলের ফোটাকে কল্পনাপ্রবণ ভঙ্গিতে একটি মেয়ের বিবাহোত্তর উচ্ছ্বাস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে ফুলের সৌন্দর্য ও কোমলতা প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
১১। রসময়ী মধুময়ী সুন্দরীরা বরকে কেন ঘিরে বসল? – ব্যাখ্যা কর।
এই বাক্যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরীরা বলতে মৌমাছি বা প্রজাপতির মতো মধুরসপ্রেমী প্রজাপতির দলকে বোঝানো হয়েছে। তারা ফুল-বরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। বাস্তবেও ফুলে যারা মধু সংগ্রহ করে, তারা ফুলের গন্ধ ও রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লেখক এই ঘটনাকে একটি রোমান্টিক বিয়ের দৃশ্য হিসেবে দেখিয়েছেন। এটি যেন বরকে ঘিরে রাখা কিছু সুন্দরী আত্মীয়ার মতো, যারা বরকে দেখে আনন্দিত। এতে কল্পনা ও প্রকৃতি একত্রে মিশে এক রঙিন ছবি তৈরি হয়েছে।
১২। ঝুমকো ফুলকে বড় মানুষের গৃহিণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?
ঝুমকো ফুল সাধারণত ঝুলে থাকে, দেখতে রাজকীয় ও আভিজাত্যপূর্ণ। লেখক তাকে বড়লোকের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ তার সাজসজ্জা ও ভঙ্গিমা গম্ভীর ও গৌরবময়। সে নিজেকে অত্যন্ত রুচিসম্পন্নভাবে উপস্থাপন করে, অন্যদের থেকে আলাদা মনে করে। এই আচরণই সমাজে বড় লোকের স্ত্রীর আচরণের সাথে মিল পাওয়া যায়। এতে কল্পনার মাধ্যমে ফুলের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি একটি সূক্ষ্ম সামাজিক ব্যঙ্গও প্রকাশ পেয়েছে।
১৩। “সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?”—লেখকের এই ভাবনার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গল্পের শেষে লেখক ফুলের বিবাহের রঙিন, কল্পনাময় দৃশ্যের কথা স্মরণ করে এই প্রশ্ন করেছেন। বিয়ের আনন্দ, হাসি, গান, আলো, সুবাস—সব মিলিয়ে এক স্বপ্নের মতো রাত কেটে গেছে। বাস্তবে এমন দৃশ্যের আর কোনো চিহ্ন নেই। তাই লেখক আবেগ নিয়ে ভাবছেন—সেই সুন্দর পুষ্পবাসর কোথায় মিলিয়ে গেল! এটি প্রকৃতির অস্থায়িত্ব, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীকও। লেখকের মনে যেন একধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেই স্মৃতির কথা ভেবে।
১৪। “সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে”—এখানে ‘বর কন্যা’ দ্বারা লেখক কাদেরকে নির্দেশ করেছেন?
এখানে ‘বর কন্যা’ বলতে লেখক কল্পনার গোলাব ও মল্লিকা ফুলকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই দুটি ফুলকে তিনি বর ও কন্যারূপে কল্পনা করেছেন এবং তাদের বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। গল্পের শেষে দেখা যায়, তারা একটি মালায় গাঁথা রয়েছে। সেই মালা লেখকের হাতেই আছে—এটা বলেই তিনি বুঝিয়েছেন, তারা আজও তার স্মৃতিতে জীবিত। এতে ফুলের প্রতি লেখকের আবেগ ও কল্পনার গভীরতা ফুটে উঠেছে।
১৫। “দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে”—লেখক এ কথাটি কেন বলেছেন?
এই কথায় লেখকের কল্পনাময় বিবাহের পরিণতির প্রতি তার টান প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে গোলাব ও মল্লিকা ফুলকে বর-কন্যা রূপে কল্পনা করে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এখন সেই ফুলদ্বয় একটি মালায় গাঁথা হয়ে আছে, যা লেখক সংরক্ষণ করেছেন। এতে বোঝা যায়, তার কল্পনার বর-কন্যা আজও তার সাথেই আছে। এটি তার স্মৃতিচারণ, আবেগ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসার প্রতীক।
১৬। বরপক্ষের বিপদ কেন—ব্যাখ্যা কর।
গল্পে বরপক্ষের বিপদ বলতে বোঝানো হয়েছে ফুলের বিয়েতে আসা পক্ষের ওপর প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি। যেমন, মৌমাছিরা আসতে পারে না, ঝড়-জলের ভয় আছে, আবার পিঁপড়ার আক্রমণের আশঙ্কা। এছাড়াও কনে যদি মুখ না দেখায়, তবে বর আসতে অনীহা প্রকাশ করে। ফুলের বিয়ে নিয়ে এমন হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করে লেখক কল্পনাকে মজার রূপ দিয়েছেন। এতে সামাজিক বিয়ের নানা টানাপোড়েনের প্রতিফলনও দেখা যায়।
১৭। লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খোলে না কেন?
ফুল-কন্যা এখানে নারীসুলভ লজ্জা ও সংযমের প্রতীক। সে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখে। এটি বাংলার গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী আচরণকেই তুলে ধরে। লজ্জা নারীর গহনা—এই ধারণাকে মজার ছলে লেখক তুলে ধরেছেন। কল্পনাজনিত হলেও, ফুলের এই লজ্জাশীলতা মেয়েদের সৌন্দর্য ও শালীনতাকে রূপকভাবে তুলে ধরে। তাই সে ঘোমটা খোলেনি।
১৮। ‘ফুলের বিবাহ’ গল্পে ‘মধু’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
এখানে ‘মধু’ বলতে বোঝানো হয়েছে ফুলের রসে থাকা মিষ্টি ও সৌরভপূর্ণ উপাদান। এটি শুধু মৌমাছির জন্য আকর্ষণ নয়, বরং কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের রসও। মধু যেন ফুলের ভালোবাসা ও রসায়নের প্রতীক। বর-কন্যার মিলনে এই মধুর ভাবনাটি লেখক কল্পনার রঙে রাঙিয়েছেন। এছাড়াও, ‘মধু’ শব্দটি আনন্দ, সুখ এবং নবদম্পতির মধুর সম্পর্ককেও বোঝায়।
১৯। ভ্রমররাজ ঘটক কীভাবে মল্লিকা ফুলের বিয়ে স্থির করলেন? বর্ণনা কর।
ভ্রমররাজ বা মৌমাছিরা গল্পে ঘটকের ভূমিকায় আসে। তারা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, সুবাস খোঁজে এবং অবশেষে বর ও কন্যাকে পছন্দ করে। মল্লিকা ফুলের কোমলতা, রূপ ও সুবাসে তারা মুগ্ধ হয়ে তাকে কন্যারূপে নির্বাচিত করে। এরপর তারা গোলাবকে পছন্দ করে, কারণ সে কুলীন, রূপবান এবং সুবাসে ভরপুর। এভাবে তারা দুটি ফুলের মধ্যে মিল খুঁজে বিয়ে স্থির করে। এটি কল্পনার মাধ্যমে একটি মৌমাছির ঘটক রূপায়ণ।
২০। বর হিসেবে গোলাবের গুণ কেমন? বর্ণনা কর।
গোলাব ফুল বা গোলাপ বর হিসেবে রূপবান, সুবাসময় এবং রাজকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সে কুলীন বংশের প্রতিনিধি, অর্থাৎ তার জাত-পরিচয় ভালো। তার রং উজ্জ্বল, গন্ধ মিষ্টি, ও সৌন্দর্য আকর্ষণীয়। গল্পে তাকে গন্ধোপাধ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ গন্ধের রাজা। তার উপস্থিতিতেই ফুলকন্যা হাসিতে ভরে ওঠে। সব মিলিয়ে বর হিসেবে গোলাব আদর্শ ও আকর্ষণীয়।