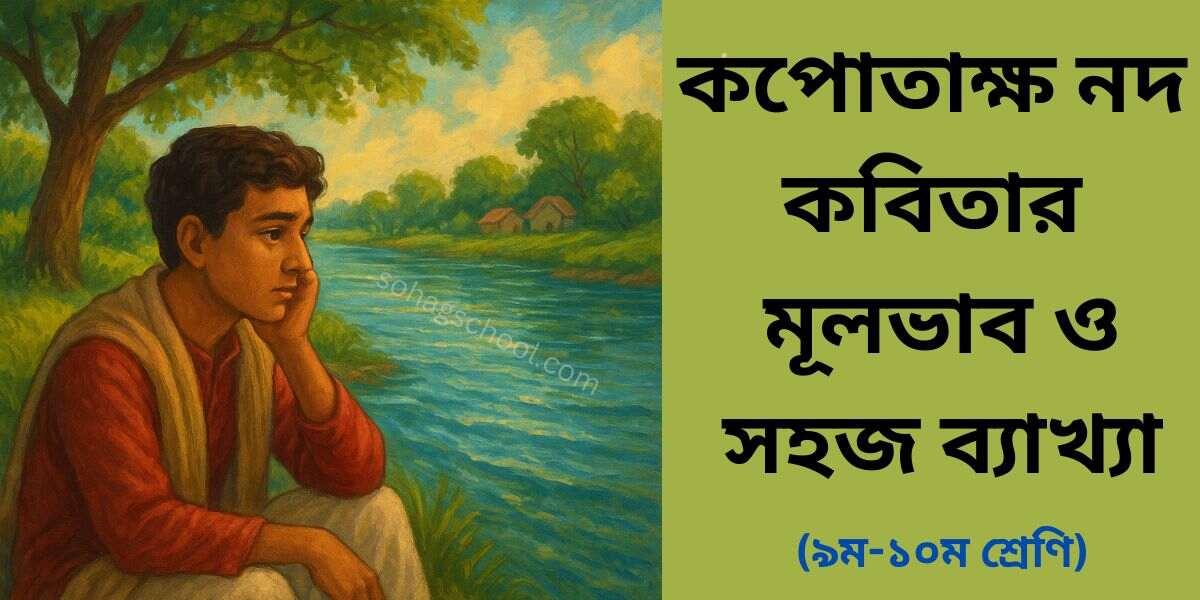মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর সনেট ‘কপোতাক্ষ নদ’ প্রবাস-জীবনের এক গভীর আবেগময় দলিল। ফ্রান্সে অবস্থানকালে তিনি নিজের জন্মভূমি যশোরের কপোতাক্ষ নদকে স্মরণ করে এই সনেট লিখেছিলেন। এই পোস্টে কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা লিখে দিলাম।
Table of Contents
কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূলভাব
মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রিয় জন্মভূমি যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে কপোতাক্ষ নদের ধারে শৈশব কাটিয়েছিলেন। পরে তিনি বিদেশে চলে যান, এবং ফ্রান্সে বসবাস করার সময় নিজের দেশ ও শৈশবের স্মৃতি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তখন তিনি কপোতাক্ষ নদকে গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করেন। কবির মনে পড়ে সেই নদীর কলকল শব্দ, যার ধ্বনি যেন এখনো তাঁর কানে বাজে। তিনি বলেন, অনেক দেশে ঘুরেও এমন স্নেহের নদী তিনি আর কোথাও পাননি। এই নদীর জলে তাঁর মনের তৃষ্ণা মেটে, কারণ নদীটি যেন মায়ের মতো স্নেহময়। তাই তিনি ভাবেন, আর কখনো কি দেখা হবে প্রিয় নদীর সঙ্গে? দূরে বসেই তিনি নদীটিকে বন্ধুর মতো ডাকেন। তার কাছে অনুরোধ করেন যেন তার ভালোবাসার কথা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। কবির এই ভালোবাসা যেন প্রবাস থেকে জন্মভূমির প্রতি কাতর হৃদয়ের প্রকাশ। নদীকে তিনি শুধু প্রকৃতি হিসেবে দেখেন না, বরং নিজের আত্মার এক অংশ হিসেবে অনুভব করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, দেশ থেকে দূরে গেলেও জন্মভূমির টান ভুলে থাকা যায় না। কপোতাক্ষ নদ তাঁর কাছে শৈশবের সঙ্গী, ভালোবাসার প্রতীক। কবিতায় ফুটে উঠেছে স্মৃতির মায়া, দেশপ্রেম আর হৃদয়ের গভীর টান।
কপোতাক্ষ নদ কবিতার ব্যাখ্যা
“সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;”
কবি এখানে তাঁর শৈশবের নদী কপোতাক্ষকে সম্বোধন করছেন। তিনি বলছেন, হে নদী! তুমি সর্বদা, সবসময় আমার মনে ভেসে ওঠো। আমি যেখানে থাকি না কেন, যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার স্মৃতি আমার মনকে ঘিরে থাকে। বিশেষ করে যখন আমি একান্ত নিরিবিলিতে থাকি, তখন তোমার কথা আরও গভীরভাবে মনে পড়ে। প্রবাসে বসে কবি নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। সেই নিঃসঙ্গতার সময়ে তিনি যেন শৈশবের দিনগুলিকে মনে করতে থাকেন। যখন তিনি জন্মভূমির সেই নদীর তীরে খেলেছেন, হেঁটেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন।
“সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে”
কবি বলছেন, হে কপোতাক্ষ নদ! আমি সবসময় তোমার কথা ভাবি। তোমার কলকল ধ্বনি আমার কানে বাজতে থাকে। সেটা এমন যেন, কোনো মানুষ রাতের ঘুমে স্বপ্নের ভেতর এক অদ্ভুত মায়াময় মন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পায়। এখানে কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে তুলনা করেছেন স্বপ্নের সাথে। প্রবাসে থেকেও মধুসূদনের মনে হয়, তিনি যেন সত্যিই কপোতাক্ষ নদীর কলকল ধ্বনি শুনছেন। আসলে তিনি নদীর কাছে নেই, কিন্তু তার স্মৃতি এত গভীর যে তা স্বপ্নের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠে।
“জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,”
কবি বলছেন, হে কপোতাক্ষ নদ! প্রবাসে থেকেও আমি যেন তোমার কলকল ধ্বনি শুনতে পাই। যদিও জানি এটা বাস্তব নয়, কেবল আমার কল্পনা বা ভ্রম (ভ্রান্তি), তবুও সেই ধ্বনির ভ্রম-স্মৃতি আমার কানে এক অপার শান্তি এনে দেয়। এই ভ্রান্তির মাধ্যমে আমি আমার মনকে সান্ত্বনা দিই, একাকীত্বের যন্ত্রণা দূর করি। এরপর তিনি বলেন, আমি বহু দেশ ভ্রমণ করেছি, অনেক নদী-নালা, ঝরনা আর প্রবাহমান স্রোত দেখেছি। কিন্তু সেসব নদীর সঙ্গেও আমার মন কখনো সেই টান অনুভব করেনি, যে টান আমি জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদীর প্রতি অনুভব করি।
“কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।”
কবি এখানে প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, আমি পৃথিবীর অনেক নদী দেখেছি, তাদের সৌন্দর্যও উপভোগ করেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ের এই ভালোবাসার তৃষ্ণা অন্য কোনো নদীর জলে মেটে না। এই স্নেহতৃষ্ণা মেটাতে পারে কেবল তুমি, হে কপোতাক্ষ নদ! কারণ তুমি আমার জন্মভূমির প্রতীক, তুমি সেই মায়ের মতো, যে নিজের সন্তানের ক্ষুধা মেটায় মায়ের দুধ দিয়ে। কবির দৃষ্টিতে কপোতাক্ষ নদ কেবল একটি নদী নয়, বরং তাঁর জন্মভূমির মাতৃস্নেহের প্রতীক। তাই তিনি নদীকে তুলনা করেছেন মায়ের স্তন থেকে প্রবাহিত দুধের সাথে। যেমন শিশু মায়ের দুধ পান করে শান্তি পায়, তেমনি কবির তৃষ্ণার্ত হৃদয় শান্তি পায় শুধু কপোতাক্ষ নদীর স্মৃতি ও ভালোবাসায়।
“আর কি হে হবে দেখা? – যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে”
এখানে কবি গভীর দুঃখ ও আকুলতা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, হে কপোতাক্ষ নদ! আমি কি আর কখনো তোমাকে সামনে থেকে দেখতে পারব? দিন যতই যাবে, আমি প্রবাসজীবনে ততই তোমার থেকে দূরে হয়ে যাব। হয়তো আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমার আর দেখা পাব না।
তিনি বলেন, যেভাবে প্রজা তার রাজাকে নিয়মিত কর (রাজস্ব) দেয়, তেমনি তুমি প্রতিদিন তোমার জলধারা সাগরের দিকে পাঠাও, যেন সাগরের রাজসিংহাসনে কর দিচ্ছো। এখানে নদীকে প্রজা এবং সাগরকে রাজা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
“বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে”
কবি নদীর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছেন, হে কপোতাক্ষ নদ! তুমি তোমার জলপ্রবাহকে এমনভাবে চালাও যেন তা চিরকাল বঙ্গদেশকে উপকৃত করে। “বারি-রূপ কর” বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন, নদীর জল যেন সাগরে সমানভাবে প্রবাহিত হয় এবং দেশের জন্য উপকারে আসে, ঠিক যেমন প্রজা রাজাকে কর দেয়।
এরপর কবি বলেন, এই নদীর ধারার জল যেন বাংলার মানুষের কানে এক মধুর সঙ্গীতের মতো পৌঁছায়। এটা শুধু সাধারণ সঙ্গীত নয়, বরং দেশপ্রেম, স্নেহ এবং মমতার গান, যা বন্ধু ও প্রিয়জনদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কবি চাচ্ছেন নদী তাঁর এই প্রার্থনাকে বাস্তবে রূপ দিক। জন্মভূমির মানুষ যেন নদীর কলকল ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, তাদের হৃদয়েও মাতৃভূমির প্রেম জাগ্রত হয়।
“নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে নাম তব বঙ্গের সংগীতে।”
কবি এখানে শেষবার কপোতাক্ষ নদীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন,
তোমার নাম, হে কপোতাক্ষ নদ, প্রবাসে থেকেও যেন প্রেমের সঙ্গে বাংলার সঙ্গীতে মিশে থাকে। অর্থাৎ, যেখানেই বাংলার মানুষ থাকুক, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ও স্মৃতি বজায় রাখতে, নদীর নাম যেন তাঁদের হৃদয়ে চিরকাল ধ্বনিত হয়।
আরও পড়ুনঃ বন্দনা কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা – শাহ মুহম্মদ সগীর